বর্তমান বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে জনতন্ত্র ও গণতন্ত্র

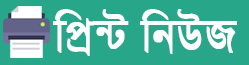
বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যার সংবিধানে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তবে স্বাধীনতার পর থেকে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চর্চা নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। সামরিক শাসন, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিভিন্ন আইনি ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কারণে গণতন্ত্র বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে (২০২৫ সাল) বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অবস্থা এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মানবাধিকার, আইনের শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এই প্রবন্ধে বর্তমান বাংলাদেশের জনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিশদ বিশ্লেষণ করা হবে। গণতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। এতে মৌলিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা, আইনের শাসন ও সুশাসন নিশ্চিত করা হয়।বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : “প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মানব মর্যাদা ও মূল্যবোধ এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হইবে।”–
জনগণের ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন। সকল নাগরিক ও রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান আইনের অধীন। জনগণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আদালত স্বাধীনভাবে কাজ করে। দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন। বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্রের ধারা বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন (বাকশাল), ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন, এবং পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছে। নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক চর্চা বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের অধীনে জাতীয় সংসদ, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়া নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে।
২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সীমিত ছিল, যা গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে সহিংসতা, অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হলো কার্যকর বিরোধী দল ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। তবে বাংলাদেশে বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত করার অভিযোগ রয়েছে। বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতার বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক সমাবেশ ও আন্দোলনে বাধা দেওয়া হয়েছে। সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা কমে গেছে, যা গণতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের একটি প্রধান স্তম্ভ হলো আইনের শাসন ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা।
প্রাসঙ্গিক চ্যালেঞ্জ: রাজনৈতিক প্রভাব: বিচার বিভাগের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন: বেআইনি আটক, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ইত্যাদি নিয়ে উদ্বেগ আছে। দ্রুত বিচার ও ন্যায়বিচারের ঘাটতি: মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও বিচারের ধীরগতি নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ।
গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো মুক্ত গণমাধ্যম ও বাকস্বাধীনতা।
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (২০১৮) সাংবাদিকদের স্বাধীনতা সীমিত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেলফ-সেন্সরশিপ: অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সরকারবিরোধী সংবাদ প্রকাশ করতে সতর্ক থাকে। নাগরিক স্বাধীনতা: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতপ্রকাশের জন্য মামলা ও গ্রেফতার বেড়েছে। সুশাসন ও দুর্নীতি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফলতার জন্য স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন অপরিহার্য। সরকারি-বেসরকারি খাতে দুর্নীতির বিস্তার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী নীতিমালা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ সীমিত। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশাসনিক সেবায় অব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষণীয়।
গণতন্ত্র সুসংহত করার উপায় : সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করা। শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা। নির্বাচনে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন বা বাতিল করা। সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। গণমাধ্যমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমানো। দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া। সরকারি খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন গঠন করা। প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার করা। যুবসমাজ ও সাধারণ জনগণের গণতান্ত্রিক চর্চায় সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা
বাংলাদেশের বর্তমান গণতন্ত্রের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে হলে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক কাঠামো, নির্বাচনব্যবস্থা, মানবাধিকার, প্রশাসনিক কার্যক্রম, এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। এ প্রবন্ধের আগের অংশে আমরা বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা আরও গভীরে গিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে পর্যালোচনা করব। বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতন্ত্র, যেখানে সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী ক্ষমতার সর্বোচ্চ নেতা। তবে বাস্তবিক অর্থে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কতটা কার্যকরভাবে গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শ মেনে চলছে, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি গণতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের প্রধান নির্বাহী (প্রধানমন্ত্রী) অত্যন্ত শক্তিশালী, ফলে নির্বাহী শাখার কার্যক্রম এককেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে।
সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো আইন প্রণয়ন এবং সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা। বর্তমানে সংসদ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ বিরোধী দলের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ। সংসদীয় বিতর্ক কমে গেছে, যার ফলে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের মতামত পর্যাপ্তভাবে প্রতিফলিত হয় না।
বাংলাদেশে প্রধানত দুটি বড় রাজনৈতিক দল সক্রিয়: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এই দুটি দলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলমান, যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের অভাব গণতন্ত্রের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক সহিংসতা ও দমননীতি: বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজের ওপর দমন-পীড়নের অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি দমন করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করা হয় বলে সমালোচনা রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো নির্বাচন। তবে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। সাম্প্রতিক জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা কম থাকে। কিছু ক্ষেত্রে ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।
EVM ব্যবহারের বিরুদ্ধে নানা বিতর্ক রয়েছে। বিরোধী দলগুলোর দাবি, EVM-এর মাধ্যমে কারচুপি করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার ব্যবস্থার ওপর সরকারি প্রভাব রয়েছে বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, অথচ সাধারণ মানুষের মামলা বছরের পর বছর ধরে আটকে থাকে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সরকারবিরোধী মত প্রকাশ করলে মামলা ও গ্রেফতারের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সাংবাদিক, বিরোধী দল ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। গণতন্ত্রের একটি মূল স্তম্ভ হলো মুক্ত গণমাধ্যম। তবে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সীমিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।
সরকার-বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করলে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো চাপে পড়ে। কিছু টেলিভিশন ও সংবাদপত্র সরকারের অনুকূলে থাকার কারণে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ২০১৮ সালে প্রণীত এই আইন ইন্টারনেটে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করেছে। এই আইনের অধীনে অনেক সাংবাদিক ও নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেক সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক চাপের কারণে সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে সাহস পায় না। গণতন্ত্র শুধু কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়, এটি স্থানীয় পর্যায়েও কার্যকর হতে হবে।
প্রধান সমস্যা: ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বেশি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সাধারণ মানুষ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারে না। স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি দমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সরকারি প্রতিষ্ঠানে ঘুষ ও অনিয়ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে নাগরিক সেবা পেতে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়ে। ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতি প্রশাসনে দুর্নীতির অন্যতম কারণ। বড় বড় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সব সময় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। দুর্নীতিবাজদের শাস্তির হার তুলনামূলক কম।
বাংলাদেশে গণতন্ত্র টিকে থাকলেও তা কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য এখনো অনেক কাজ বাকি। স্বচ্ছ নির্বাচন, কার্যকর সংসদ, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, মুক্ত গণমাধ্যম ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠনের মাধ্যমেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র টিকে আছে, তবে তা কার্যকর ও শক্তিশালী গণতন্ত্র হয়ে উঠতে হলে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন এবং সুশাসন নিশ্চিত করা না গেলে গণতন্ত্র দুর্বল হতে পারে। জনগণের অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। দেশ এগিয়ে নিতে হলে দায়িত্বশীল রাজনীতি, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলা জরুরি।
লেখক পরিচিতি : উজ্জ্বল হোসাইন, লেখক ও সাংবাদিক, চাঁদপুর।
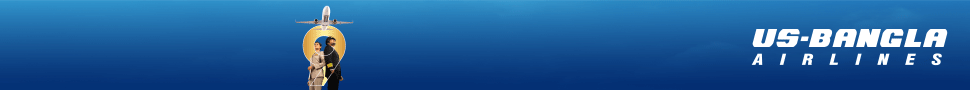













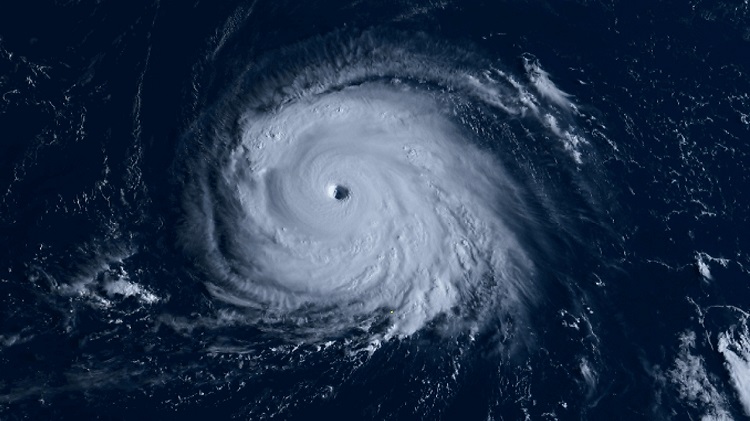

আপনার মতামত লিখুন