মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের বিরোধী : ফিরে আসবে ভয়ের সংস্কৃতি

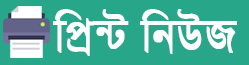
মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশের প্রধান চালিকা শক্তি হলো মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক সমাজব্যবস্থা এই দুই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই মুক্তচিন্তার উপর দমননীতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখনই সমাজে স্থবিরতা নেমে এসেছে, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আধুনিক যুগেও বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দমনমূলক সংস্কৃতি পুনরায় ফিরে আসছে। ভয় ও নিপীড়নের এই সংস্কৃতি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নতুন কোনো ধারণা নয়। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বিভিন্ন সময় এই অধিকার রক্ষার জন্য ব্যক্তি ও সমাজকে বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। প্রাচীন গ্রিসে সক্রেটিস মুক্তচিন্তার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার অনুসন্ধিৎসু মনোভাব ও প্রচলিত বিশ্বাসকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা শাসকদের জন্য হুমকি হয়ে ওঠে। ফলে, তাকে হেমলক বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়। রেনেসাঁ যুগে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতার মুখে পড়েন, কারণ তিনি সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করেছিলেন। তাকে বাধ্য করা হয়েছিল নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করতে, যা মুক্তচিন্তার বিরুদ্ধে দমননীতির একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।
মুক্তচিন্তা হলো এমন একটি মানসিক প্রবণতা, যেখানে ব্যক্তি নিজস্ব যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাস ও মতামত গড়ে তোলে, বাইরের চাপ বা প্রচলিত মতামতের উপর নির্ভর না করে। অন্যদিকে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হলো সমাজের যে কোনো বিষয় নিয়ে দ্বিধাহীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার, যা ব্যক্তি ও গণমাধ্যম উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এই দুই নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি যখন মুক্তভাবে চিন্তা করতে পারে, তখনই নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পথ উন্মোচিত হয়। আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে গণতন্ত্র সুসংহত হয়, কারণ জনগণ সরকারের কার্যক্রম নিয়ে কথা বলতে পারে এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে পারে।
বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে ও সমাজে মুক্তচিন্তার বিরোধী শক্তিগুলো আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই প্রবণতার পেছনে কাজ করছে— স্বাধীন মতপ্রকাশ ও মুক্তচিন্তা সবসময়ই স্বৈরাচারী শাসকদের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ গণতান্ত্রিক পরিসরে প্রশ্ন তোলা হলে তাদের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়। ফলে, তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে— যেমন, বিরোধী মত দমন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করা এবং ডিজিটাল নজরদারির মাধ্যমে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করা। মুক্তচিন্তা অনেক সময়ই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও রাজনৈতিক উগ্রবাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশে দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দল বা প্রভাবশালী ধর্মীয় গোষ্ঠী মুক্তচিন্তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে, মুক্তচিন্তকদের অনৈতিক বা অবিশ্বাসী বলে আক্রমণ করে। ফলস্বরূপ, সমাজে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যেখানে মানুষ মুক্তভাবে চিন্তা ও মতপ্রকাশ করতে সাহস পায় না। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সামাজিক মাধ্যম মুক্ত মতপ্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু একইসঙ্গে এটি ভুল তথ্য প্রচার ও মতপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক সরকার ও রাজনৈতিক দল সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রল বাহিনী নিয়োগ করে মুক্তচিন্তকদের হেনস্তা করে, তাদের মতপ্রকাশের সুযোগ সংকুচিত করে দেয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অন্যতম মাধ্যম হলো গণমাধ্যম। কিন্তু অনেক দেশে সাংবাদিকদের উপর নির্যাতন, হত্যার হুমকি এবং গ্রেফতারের মতো ঘটনাগুলো ঘটছে। এর ফলে, সাংবাদিকরা সাহসী প্রতিবেদন প্রকাশ করতে ভয় পায় এবং স্বাভাবিকভাবেই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন থেকে যায়। ভয়ের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম পদ্ধতি হলো জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। যখন নাগরিকরা দেখে যে, সরকারের সমালোচনা করলে কারাবরণ বা আক্রমণের শিকার হতে হয়, তখন তারা নিজেদের মতপ্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে, ক্ষমতাসীনরা এক ধরনের স্ব-নিয়ন্ত্রিত নিপীড়নব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়।
ভয়ের সংস্কৃতি ও সমাজের উপর প্রভাব : মুক্তচিন্তার দমন এবং ভয়ের সংস্কৃতির বিস্তার সমাজের উপর বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে—যে সমাজে মুক্তচিন্তা নেই, সেখানে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও প্রযুক্তির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করার পরিবেশ না থাকলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে না, ফলে সামগ্রিক অগ্রগতি শ্লথ হয়ে যায়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর থাকে না। যখন জনগণের কণ্ঠরোধ করা হয়, তখন শাসকদের জবাবদিহিতা কমে যায় এবং একনায়কত্বের পথ সুগম হয়। ভয়ের সংস্কৃতি সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে জনগণ তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে না, ফলে ক্ষোভ জমতে জমতে একসময় সহিংসতায় রূপ নেয়। মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের দমন মানবাধিকারের অন্যতম গুরুতর লঙ্ঘন। এটি ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে দমনমূলক ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়।
মুক্তচিন্তা রক্ষার উপায় : মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে—গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুসংহত থাকলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করা সহজ হয়। শক্তিশালী বিচারব্যবস্থা ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে সাংবাদিকদের সুরক্ষা দিতে হবে এবং সংবাদপত্র ও অনলাইন মাধ্যমের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমাতে হবে। একটি সমাজে মুক্তচিন্তা বিকাশের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্তিবাদ, আলোচনা ও বিতর্কের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নাগরিকদের সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মানবাধিকার সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীদের এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।
১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও মতপ্রকাশের অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে এই অধিকার সংকুচিত করা হচ্ছে, যা গণতন্ত্রের জন্য গুরুতর হুমকি। বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপট ১. চীন : চীনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। ইন্টারনেট সেন্সরশিপ (গ্রেট ফায়ারওয়াল) এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার জন্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৯ সালের তিয়েনআনমেন স্কয়ার গণহত্যার কথা উল্লেখ করা নিষিদ্ধ, এবং যারা বিষয়টি নিয়ে কথা বলে, তাদের জেলে পাঠানো হয়। ২. রাশিয়া : রাশিয়ায় ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীন সাংবাদিক ও বিরোধী নেতারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় প্রচারণার মাধ্যমে ভিন্নমতকে দমন করা হয়। ৩. মধ্যপ্রাচ্য : মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় এবং গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ৪. বাংলাদেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশ : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ব্লগার, লেখক ও সাংবাদিকদের উপর হামলা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন দমনমূলক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মতপ্রকাশের সুযোগ সীমিত করা হচ্ছে।
ভয়ের সংস্কৃতির চক্র, ভয়ের সংস্কৃতি ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ধাপ : সরকার বা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ভিন্নমতের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। দ্বিতীয় ধাপ : স্বাধীন সাংবাদিক, লেখক, মানবাধিকার কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। তৃতীয় ধাপ : সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে তারা সাহস করে কিছু বলতে না পারে। চতুর্থ ধাপ : রাষ্ট্রীয় নীতিতে স্বৈরাচারী মনোভাব দৃশ্যমান হয় এবং মতপ্রকাশের সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।
মুক্তচিন্তার দমন রোধে করণীয় : আইনের শাসন কার্যকর হলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব। বিচারব্যবস্থা স্বাধীন হলে নাগরিকরা নির্ভয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে জনগণ সত্যিকারের তথ্য পায় এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। শিক্ষায় মুক্তবুদ্ধি ও প্রশ্ন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, যাতে মানুষ চিন্তা করতে শেখে এবং সহজেই প্রভাবিত না হয়। মানবাধিকার সংগঠন, এনজিও, নাগরিক আন্দোলন এসব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আঘাত মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে, যখনই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে, তখনই সমাজ স্থবির হয়েছে, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পিছিয়ে গেছে। ভয়ের সংস্কৃতি ধ্বংসাত্মক এবং তা দমন করতে হলে গণতন্ত্র, আইন, শিক্ষা ও নাগরিক সচেতনতার বিকাশ ঘটাতে হবে। মুক্তচিন্তা রক্ষার লড়াই কখনো থামানো যাবে না, কারণ এর উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।
মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি সমাজের অন্যতম মৌলিক অধিকার। যখনই এই অধিকার সংকুচিত হয়, তখনই সমাজ পিছিয়ে পড়ে এবং দমনমূলক ব্যবস্থা চালু হয়। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভয়ের সংস্কৃতি সৃষ্টি করছে। তবে, ইতিহাস সাক্ষী যে, জনগণ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে দমনমূলক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। এজন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা, শিক্ষার প্রসার এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই আমরা ভয়কে জয় করে মুক্তচিন্তার সমাজ গড়ে তুলতে পারবো।
লেখক পরিচিতি : উজ্জ্বল হোসাইন, লেখক ও সাংবাদিক, চাঁদপুর।
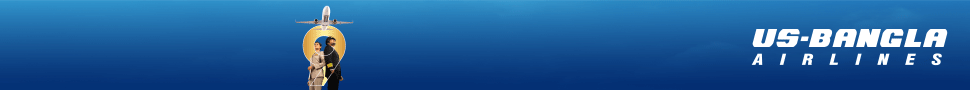






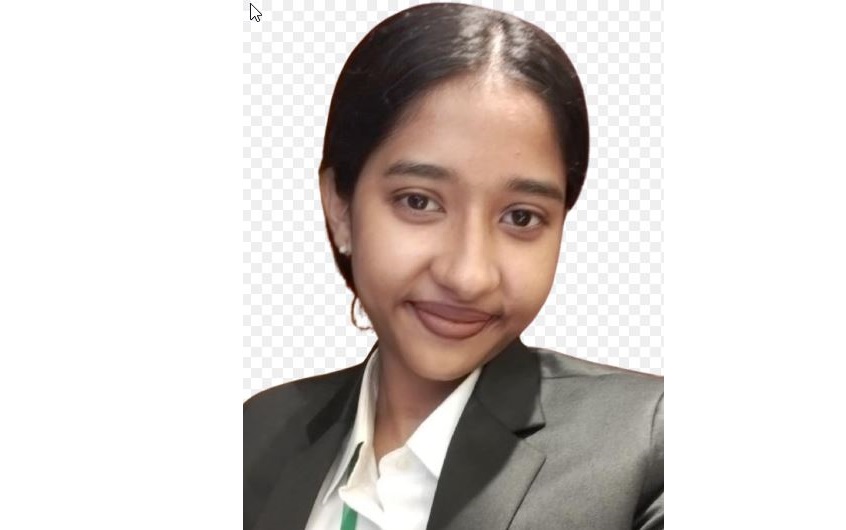











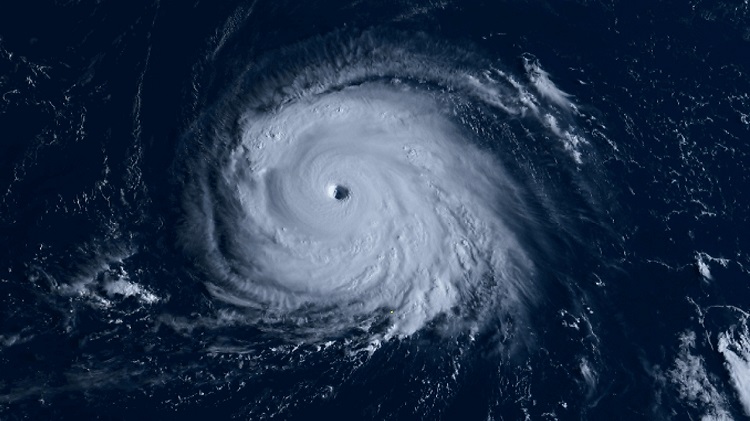

আপনার মতামত লিখুন