বাংলায় নারীবাদী সাহিত্য ও নারীদের অধিকার

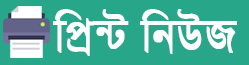
বাংলা সাহিত্য যুগে যুগে সমাজের পরিবর্তন, বিশেষ করে নারীদের অবস্থানের প্রতিচিত্র তুলে ধরেছে। নারীবাদী সাহিত্য এমন এক সাহিত্যধারা, যা নারীর অধিকার, সমানাধিকারের সংগ্রাম, সমাজের পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা এবং নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প বলে। বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী চিন্তাধারা এক নতুন যুগের সূচনা করেছে, যা নারীদের অধিকার আদায়ের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
নারীবাদী সাহিত্য এমন এক সাহিত্য, যেখানে নারীর অধিকার, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য, পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নারীর আত্মপরিচয়কে তুলে ধরা হয়। এই সাহিত্যধারার মূল উদ্দেশ্য হলো নারীর বঞ্চনার ইতিহাসকে সামনে আনা এবং নারীর স্বাধীনতার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা।
নারীবাদী সাহিত্য শুধুমাত্র নারীদের জন্য লেখা হয় না; বরং এটি সমাজের জন্য এক নতুন চেতনার বার্তা বহন করে। এটি কেবল পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা নয়, বরং একটি সমতার সমাজ গড়ার আহ্বানও বটে।
বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বে নারীর অবস্থা ছিল গৌণ। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নারীদের উপস্থিতি খুবই কম। মূলত পুরুষ লেখকদের হাতেই সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, যেখানে নারী চরিত্রগুলোকে প্রধানত পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করা হতো।
চন্দ্রাবতী (১৫৫০-১৬০০ খ্রি.) ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারী কবি, যিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখায় নারীর দুঃখ-কষ্ট, প্রেম, এবং সমাজের কঠোরতা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।
উনবিংশ শতাব্দী ছিল বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের যুগ, যখন নারীরা ধীরে ধীরে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার সুযোগ পেতে শুরু করেন। এই সময়ে কিছু সাহিত্য নারীদের অধিকার ও সমতার প্রশ্ন তোলে।
বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী চেতনার প্রথম ও অন্যতম প্রধান রূপকার। তাঁর সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫) এক অনন্য বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, যেখানে নারীরা সমাজের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয় এবং পুরুষরা অবরুদ্ধ থাকে। এই রচনা নারীর সম্ভাবনা ও স্বাধীনতার প্রতীক।
তাঁর অবরোধবাসিনী গ্রন্থে মুসলিম নারীদের অবরুদ্ধ জীবনের নির্মম বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর লেখনী শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, বরং এক সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।
আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) ছিলেন নারীবাদী সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসত্রয়ী—১. প্রথম প্রতিশ্রুতি ২. সুবর্ণলতা ৩. বকুল কথা
এই উপন্যাসগুলোতে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজে নারীর স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয়ের জন্য সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর লেখায় নারীশিক্ষা, কুসংস্কার ও সমাজের বাধা অতিক্রম করে নারীর এগিয়ে যাওয়ার গল্প বলা হয়েছে।
মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) ছিলেন একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক, যিনি আদিবাসী ও নিম্নবর্গীয় নারীদের জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। তাঁর হাজার চুরাশির মা উপন্যাসে রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকা এবং রাষ্ট্রদ্রোহের শিকার হওয়া এক মায়ের মানসিক অবস্থা চিত্রিত হয়েছে। তাঁর অরণ্যের অধিকার, স্তনদায়িনী প্রভৃতি রচনায় সমাজের প্রান্তিক নারীদের দুর্দশা ও নারীর শোষণের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে।
সেলিনা হোসেন (জন্ম ১৯৪৭) বাংলা সাহিত্যে নারীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর হাঙর নদী গ্রেনেড মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক চিত্র।
তসলিমা নাসরিন (জন্ম ১৯৬২) নারীবাদী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখিকা, যিনি পিতৃতন্ত্র ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর লজ্জা, আমার মেয়েবেলা, নির্বাসন প্রভৃতি গ্রন্থে নারীর অধিকার, সামাজিক নিপীড়ন ও প্রথাগত ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদ রয়েছে।
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (১৯৫০-২০১৫) উপন্যাসগুলোতে শহুরে নারীদের বাস্তবতা ও সামাজিক টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। দহন, অলিখিত, কাছের মানুষ প্রভৃতি রচনায় নারীর আত্মপরিচয় ও সামাজিক অবস্থানের সংকট ফুটে উঠেছে।
বাংলা নারীবাদী সাহিত্য শুধুমাত্র কল্পকাহিনি নয়; বরং এটি নারীদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নারীবাদী লেখকেরা তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে নারীর শিক্ষার অধিকার, কর্মসংস্থানের সুযোগ, পারিবারিক ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন।
নারী শিক্ষা একটি সমাজের সামগ্রিক উন্নতির মূল ভিত্তি। একজন শিক্ষিত নারী শুধু নিজের উন্নতি করেন না, বরং পুরো সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং স্বাস্থ্যখাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।
শিক্ষিত নারী পরিবার ও সমাজে সচেতনতার প্রসার ঘটায়, যা শিশুশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
শিক্ষিত নারীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, যার ফলে পরিবার ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। নারীরা স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন হয়, যা শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে সাহায্য করে। শিক্ষা নারীদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। নারী শিক্ষা লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে এবং সমাজে সমান সুযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে। নারী শিক্ষার প্রসারের পথে বাধা, দারিদ্র্য ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা, সামাজিক কুসংস্কার ও প্রথা, বাল্যবিবাহ, নিরাপত্তার অভাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপর্যাপ্ততা এসব নারীদের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়ায়।
নারী শিক্ষার প্রসারে করণীয় : শিক্ষাবৃত্তি, উপবৃত্তি এবং বিনামূল্যে বই-খাতা বিতরণের মাধ্যমে নারীদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা। গণমাধ্যম, সামাজিক প্রচারণা ও কমিউনিটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে নারী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা। মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট, নিরাপদ বিদ্যালয় এবং পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল ক্লাসরুম এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নারী শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করা। বাল্যবিবাহ ও নারীদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা।
নারী শিক্ষার প্রসার কেবল একটি জাতির নয়, পুরো বিশ্বের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সরকার, সমাজ এবং প্রতিটি পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নারীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে, যাতে তারা সমাজের মূলধারায় সমানভাবে অংশ নিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করতে পারে।
নারীর আইনগত অধিকার ও সচেতনতা নিশ্চিত করা একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন নারীদের সুরক্ষা, সমতা এবং ক্ষমতায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তবে, অনেক নারী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, যার ফলে তারা বিভিন্ন সামাজিক ও আইনি সমস্যার শিকার হয়। নারীর মৌলিক আইনগত অধিকার- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের শিক্ষার অধিকার রয়েছে। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে সরকার বিনামূল্যে শিক্ষা, উপবৃত্তি এবং শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। নারীদের পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকার রয়েছে, যা ধর্মীয় ও পারিবারিক আইনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। মুসলিম আইন, হিন্দু আইন ও বিশেষ বিবাহ আইনের ভিত্তিতে নারীদের সম্পত্তির অধিকার বিভিন্ন রকম হতে পারে। বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত অধিকার বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী, মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইন, ১৯৩৯ অনুযায়ী, নারীরা বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারে এবং তালাকপ্রাপ্ত হলে নির্দিষ্ট হক ও অধিকার পায়। পারিবারিক আদালতের মাধ্যমে নারীরা মোহরানা, খোরপোষ ও সন্তানদের অভিভাবকত্বের দাবি করতে পারে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী, নারী-পুরুষের সমান মজুরির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে ২০১০ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসারে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অনুযায়ী, ধর্ষণ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ও পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। দণ্ডবিধি ৪৯৭ ধারা অনুযায়ী, নারীদের প্রতি সহিংসতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী, যৌতুক প্রদান ও গ্রহণ উভয়ই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
নারীদের জন্য বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ সেবা বৃদ্ধি করা। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে আইন সচেতনতামূলক কর্মশালা পরিচালনা করা। টেলিভিশন, রেডিও, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারী অধিকার নিয়ে প্রচার চালানো। নারীদের জন্য বিশেষ সচেতনতা ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে নারী অধিকার ও আইন বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা। জয় ফোন (১০৯) – নারী ও শিশুদের সহায়তা প্রদানের জন্য একটি সরকারি হেল্পলাইন। বিভিন্ন এনজিও ও সরকারি প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে আইনি সহায়তা ও কাউন্সেলিং সেবা দিচ্ছে। নারী অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সংগঠন যেমন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ব্র্যাক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
নারীর আইনগত অধিকার রক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি শুধুমাত্র নারীদের জন্য নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য কল্যাণকর। সরকার, সামাজিক সংগঠন এবং প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারবে। এছাড়া নারীরবৈবাহিক ও পারিবারিক অধিকার, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন তুলেছে। নারীর আত্মপরিচয়ের সন্ধান-নারী কেবল মা, স্ত্রী বা কন্যা নয়; বরং একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।
বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী লেখকদের অবদান অসামান্য। তাঁরা কেবল সাহিত্য রচনা করেননি, বরং সমাজে নারীদের অবস্থানকে প্রশ্ন করেছেন, পরিবর্তন এনেছেন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছেন। নারীবাদী সাহিত্য নারী জাগরণ ও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
ভবিষ্যতে নারীবাদী সাহিত্য আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং সমাজে নারীর সমানাধিকারের প্রশ্নকে আরও গভীরভাবে উত্থাপন করবে। বাংলা সাহিত্যে নারীদের কণ্ঠ আরও দৃঢ় হবে, যা সমাজকে আরও মানবিক ও সমতাভিত্তিক করে তুলবে।
লেখক পরিচিতি : উজ্জ্বল হোসাইন, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক, চাঁদপুর।
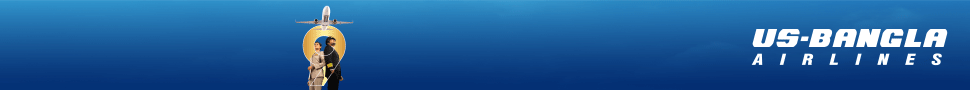

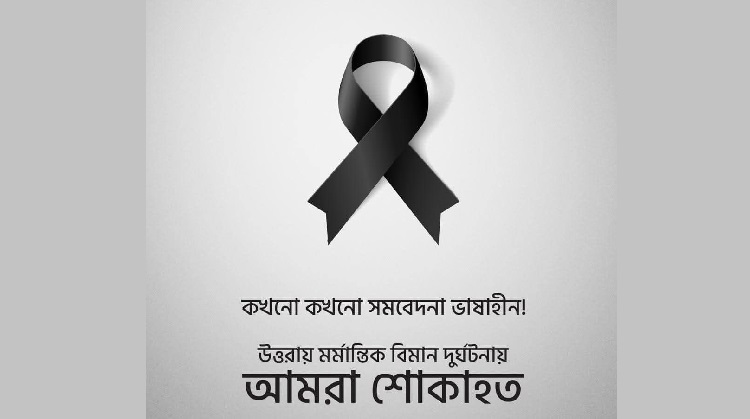





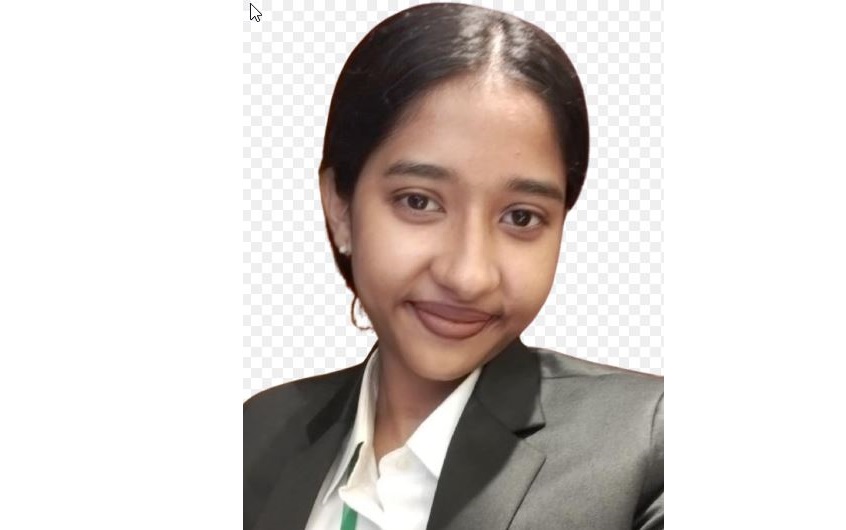











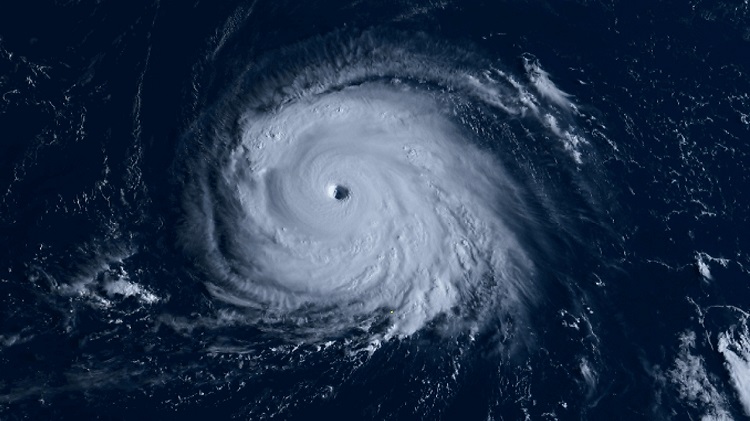

আপনার মতামত লিখুন